conservation of resource – সম্পদ সংরক্ষণ কী, সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সমূহ, মাটি সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
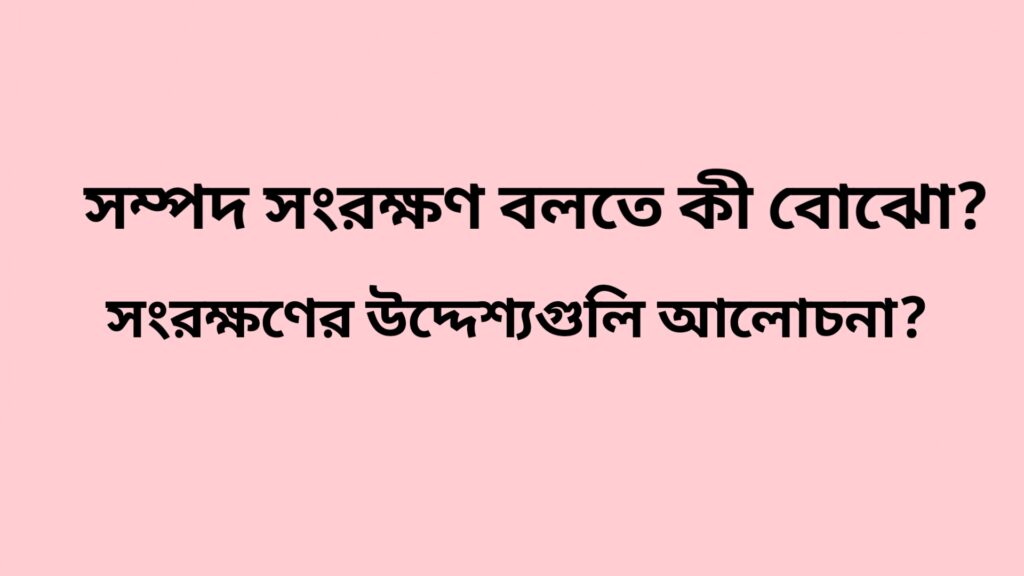
বিবর্তনের পথে পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে প্রাকৃতিক জৈব ও অজৈব সম্পদ সমূহ সংকটের সম্মুখীন হয়। মানব জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পৃথিবীর পরিবেশ মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীরা হারিয়ে যেতে থাকে। পরিবর্তে মানুষের উপকারে এবং সরাসরি কাজে লাগে এমন সব উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মানুষের দ্বারা ব্যাপকভাবে চাষাবাদ ও প্রজনন হতে থাকে।
ক্রান্তীয় অঞ্চলের বনভূমি বড় বড় কোম্পানি যারা গবাদি পশু এবং কাঠের ব্যবসা করে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সমুদ্রে অবাধে অনিয়ন্ত্রিত এবং মৎস্য শিকার সামুদ্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং খাদ্য উপযোগী মাছের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। বন্য পশু-পাখি মাংস, চামড়া ও অন্যান্য সৌখিন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য নিধন হতে থাকে। এই দামি পণ্য সামগ্রী ধনীদেশ গুলোতে চড়া দামে বিক্রি হয়।
শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে শক্তি সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতি সৌখিন জীবন যাপনের জন্য মাথাপিছু সম্পদ আহরণে উন্নয়নশীল দেশে বেড়ে যায়, আর অনুন্নত দেশগুলো এদের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে যায়। পরিবেশ থেকে অহরহ সম্পদ শোষণ করে প্রকৃতির বুকে ঢেলে দেয় বিষাক্ত দূষিত পদার্থ সমূহ।
যে সকল মানুষ, মানুষের ভবিষ্যৎ, পৃথিবী নামক এই গ্রহের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, তারা মানুষের ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ যে একান্ত প্রয়োজন তা ভাবতে শুরু করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সেই চিন্তাভাবনার ফসল। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের প্রভাব বিষয়ে আমরা P.E CLOUD (১৯৬৯) এর ডেমোগ্রাফিক কসেন্ট (Q) এর কথা স্মরণ করতে পারি।
ডেমোগ্রাফিক কোসেন্ট (Q) = লভ্য সম্পদের পরিমাণ / জনসংখ্যার ঘনত্ব × মাথাপিছু সম্পদের ব্যবহার
ডেমোগ্রাফিক ডেমোগ্রাফিক কসেন্ট (Q) নিম্নমুখী হলে জীবন যাত্রার মান নিম্নগামী হয় বলে মনে করা হয়। যেহেতু জনসংখ্যার ঘনত্ব রাশির কোন সম্ভাবনা নেই, এবং মাথাপিছু সম্পদ আহরণের মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সম্পদের পরিমাণ কমছে তাই সম্পদ সমূহকে সঠিক পরিকল্পনা সহ ব্যবহার আবশ্যিক।
সম্পদের সংরক্ষণের (conservation of resource) সংজ্ঞা
সাধারণ মানুষের চোখে যারা পরিবেশের সংরক্ষণ চাই, তারা প্রগতির পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নত জীবনযাপন দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয়। একজন মানুষ দূষিত পরিবেশে, প্রাকৃতিক সম্পদহীন অবস্থায় কোনদিন উন্নত জীবনযাপন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের সংরক্ষণ পন্থীরা অপরিকল্পিত উন্নতির বিপক্ষে। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ পরিকল্পনা ছাড়া যে কোন পরিকল্পনা সাময়িক ফলপ্রসু হলেও ভবিষ্যতে তার বিষময় পরিনাম ভোগ করতে হয়। তাই সম্পদ সংরক্ষণ কি এবং কেন, তা প্রত্যেকের জানা জরুরী কর্তব্য।
সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাসমূহ যার মাধ্যমে সম্পদের অতি ব্যবহার ও অপব্যবহার রোধ করে। সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে পূরণ করা। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণের দুটি দিক বর্তমান।
- পরিবেশের গুণমান কে ধরে রাখা যার মাধ্যমে মানুষের আর্থিক ও আর্থিক লাভ ঘটে।
- একটা সুষম ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ সমূহের ধারাবাহিক যোগান ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা।
সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দীর্ঘস্থায়ী ফলপ্রসু ব্যবহার, এবং সম্পদ সমূহের গুণমানগত বর্ধিতকরণ সংরক্ষণ একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া যার সুফল সুদূরপ্রসারী।
সংরক্ষণের উদ্দেশ্য
- বাস্তুতন্ত্রের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এবং জীবনধারক ব্যবস্থার সমূহের সাম্যবস্থা বজায় রাখা।
- জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ করা।
- সম্পদ সমূহের বিচক্ষণ ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সুফল লাভের ব্যবস্থা করা।
সম্পদ সংরক্ষণের (conservation of resource) বিষয় সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল
১) বাস্তুতন্ত্রের স্থিত অবস্থায় বজায় রাখা এবং জীবনধারক ব্যবস্থা সমূহের সাম্যবস্থা বজায় রাখা – জল, মাটি, বাতাস জীবনধারক এই তিন প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, সার, প্রভৃতি পরিবেশকে দূষিত করছে। ১৮ শতকে পৃথিবীতে বৃহৎ শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস যে দূষিত হচ্ছে বিজ্ঞানীরা তা ক্রমশ বুঝতে পারছে। ১৯৪০ সালে সাধারণ মানুষ বায়ু দূষণ সম্পর্কে সচেতন হয়। ওই বছরে আমেরিকার লস অঞ্চলেসে ব্যাপক ধোঁয়াশা দেখা দেয়। যার ফলে ১৪ হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কুড়িজন মারা যান।
কলকারখানার ধোয়া, কয়লা পোড়ানো ও যানবাহনের জ্বালানি প্রধানত বায়ু দূষণ ঘটায়। তাছাড়া জনবিস্ফোরণের সাথে সাথে কৃষি জমি এবং বসবাসের জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলস্বরূপ অরণ্য ধ্বংস হতে থাকে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এক হেক্টর অরণ্য বছরে চার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেই। এবং দুই টন বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিবেশের ত্যাগ করে। অরণ্য ধ্বংসের সাথে সাথে ভূমিক্ষয় শুরু হয়। মাটি, জল, অরণ্য সংরক্ষণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল ।
(ক) মাটি সংরক্ষণ(conservation of soil methods)
মাটি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। গাছপালার সৃষ্টি, বৃদ্ধি, মানুষ সহ অন্যান্য জীবজন্তুর বসবাস সবই মাটির উপরেই। বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা, গতিশীলতা এবং সাম্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে মাটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি একটি অপুনর্নবীকরণ সম্পদ। সময়ের সাপেক্ষে মাটির ক্ষয় বাস্তুতন্ত্রের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও কোন একটি সময়ে যে পরিমাণ মৃত্তিকা হয় ঠিক সেই পরিমাণ মাটির সৃষ্টিও হয়। ফলে মোট মাটির পরিমাণ ঠিক থাকে। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে মাটি ক্ষয়ের হার ত্বরান্বিত হচ্ছে কিন্তু গঠনের হার হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মাটির মোট পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং সংকর দেখা দিচ্ছে।
নিম্নে মাটি ক্ষয়ের কারণ উল্লেখ করা হল –
(a) অরণ্য ধ্বংস – অরণ্যের গাছপালার তাদের শিকড় দিয়ে মাটির কণাগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখে। মাটি শিকড়ের সেই বন্ধন ছিন্ন করে কোথাও যেতে পারে না। গাছপালা ভূমিক্ষয় কে রোধ করে থাকি। সাধারণত জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন হলো বেশি পরিমাণ কৃষি জমির, আসবাবপত্রের, শিল্প স্থাপনের এবং শহরবান ও নগরায়নের। ফলস্বরূপ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করতে লাগলো গাছ কেটে। এর ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। বিশেষত যেখানে এক সেন্টিমিটার মাটি তৈরি হতে কয়েকশো বা হাজার বছর সময় লাগে অপরদিকে তা ধ্বংস হতে সময় লাগে মাত্র কয়েকদিন। প্রত্যেক বছর শুধুমাত্র ভারতেই প্রায় ৬০০০ লক্ষ টন ভূমিক্ষয় হয়।
(b) কৃষিকার্য – দর্শনের পর দীর্ঘ সময় মাটিকে ফেলে রাখা ও পাহাড়ের ঢাল বরাবর ধাপ কেটে সেই ধাপ অনুযায়ী চাষ করার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধির ফলে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণও সাধারণভাবে বাড়তে থাকে। চাষ জমিতে বেশি পরিমাণ অজৈব সারের ব্যবহার ভূমিক্ষয়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়াও জমিতে জলের প্রবাহের গতির সুনির্দিষ্ট না করার ফলে ও কৃষি জমির উর্বর ওপরিতল জলশ্রুতে হ্রাস পায়।।
(c) ত্রুটিযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা – সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা ছাড়া শহর বা নগর স্থাপন, শিল্প স্থাপন কিংবা বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনাগত ত্রুটি ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়েও দাঁড়ায়।
(d) গোচারণ – অত্যাধিক পরিমাণে গোচারণে মাটির উপরের ঘাসের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে মাটি আলগা হয়ে যায় এবং ভূমিক্ষয় ঘটতে থাকে। সভ্যতার অগ্রগতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু তার পরিমাণ যাতে কমানো যায় তার জন্য করণীয় বিষয়গুলি আমাদের মনে রাখতে হবে।
মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও উর্বরতা বৃদ্ধি ~
নগরায়ন, শিল্প স্থাপন, কৃষি জমির উপর দলের মৃত্তিকার ক্ষয়, কৃষিজমের সংকোচন প্রভৃতি আগামী দিনে বিপুল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। তাই ভূমি সংরক্ষণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদক্ষেপ গুলি নিম্নরূপ –
(a) বনসৃজন – অপরিকল্পিতভাবে অরণ্য নিধন উচিত নয়। গাছ কাটার সাথে সাথে অনাচ্ছারিত স্থানে যাতে আগের থেকে গাছ লাগানো হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৫৬ সালের জাতীয় অরণ্য নীতি অনুসারে মোট অরণ্যের পরিমাণ যাতে ৩৩% এর কম না থাকে সেদিকে নজর দেয়া উচিত। পাহাড়ের ঢালে ৬৬% বনভূমি থাকলে ভূমিক্ষয় এর সম্ভাবনা কম থাকে।
কিন্তু আমাদের দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২০% এর থেকেও কম। ভূমিক্ষয় রোধ করতে সঠিক পরিকল্পনা সহকারী মাটির গঠন এবং প্রকৃতি অনুসারে বনসৃজন করা একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত অনাচ্ছাদিত পতিত স্থলভূমিকে অরণ্যে পরিবর্তিত করা একান্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকা ক্ষয় রোধে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(b) কৃষি জমির ব্যবহারের পরিবর্তন – কৃষি জমিতে শস্য আবর্তনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। এর ফলে কৃষি যোগী স্যামসাং এর জন্য কৃষিজ উদ্ভিদ দ্বারা আচ্ছাদিত থেকে থাকে। ভালো জাতীয় উদ্ভিদের চাষের মাধ্যমে জমিতে নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো যায়।
(c) যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা – কোন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে ওই জায়গার মাটির গঠন দৃঢ়তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রকল্প রূপায়ণে প্রাকৃতিক ঢাল গুলি বাদ দেয়া উচিত ঢালের সমস্ত বনজ সম্পদ রক্ষা করা উচিত।
(d) সঠিক চারণভূমি পরিচালনা – চারণ ভূমির ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ মাটির ক্ষয় রোধে সাহায্য করে। কোন জায়গাকেই স্থায়ী চারণভূমি ঘোষণা করা উচিত নয়। এবং কিছু এলাকায় গবাদিপশু চারণের উপর নিষেধ আরোপ করা উচিত।
( খ ) জল সংরক্ষণ ( conservation of resources water )
জল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ যা যা জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান। পানীয় হিসেবে, গৃহস্থলীর কাজে, শিল্পী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই মানুষের সভ্যতা নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জল সম্পদের ব্যবহারের প্রকৃতি সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ৭৩ ভাগ অংশই জল। এই জলের ৯৭.৩৯ ভাগ সামুদ্রিক নোনা জল, হ্রদ নদীতে প্রাপ্ত মিষ্টি জলের পরিমাণ মাত্র ০.০২ ভাগ। আবহাওয়া মন্ডলে জলীয় বাষ্প রূপে বর্তমান ০.০০১ ভাগ জল, মরু অঞ্চলে বরফ হয়ে জমে আছে ২.০১ ভাগ, ভূগর্ভস্থ ও মাটির কণার সঙ্গে লেগে থাকে জলের পরিমাণ ০.৫৮ ভাগ। পৃথিবীতে মোট মিষ্টি জলের পরিমাণ ২.৬ ভাগ যার মধ্যে ৭৭.২ ভাগ মরু অঞ্চলে বরফ। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল হলেও ব্যবহার যে জলের পরিমাণ খুবই অল্প।
জল সম্পদ সংকটের কারণ
জল সম্পদ সংকটের প্রধান কারণ দুটি
(ক) দূষণ ঘটিত সমস্যা – গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের পর জলে যুক্ত হয় নানা জৈব পদার্থ।, রোগ সৃষ্টিকারী জীবন, যা জলের গুণগত মানের অবনয়ন ঘটায়, কলকারখানায় সৃষ্টি দূষিত পদার্থ সমূহ যেমন পেলন, সায়ানাইড, আর্সেনিক, সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, প্রভৃতি ভারি ধাতু জলকে দূষিত করে। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক পদার্থ সমূহ স্বাভাবিক জলজ পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। এছাড়া তেল, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ, তাপীয় দূষণ প্রভৃতি ও জলের গুণগতমানকে নষ্ট করে।
( খ ) – ব্যবহার্য জলের পরিমাণগত মানের অবনতির কারণ হিসেবে বলা যায় – জলাভূমি বুঝিয়ে ফেলা, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন। ব্যবহার উপযোগী মিষ্টি জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে। বাধাহীন এবং ইচ্ছেমতো মিষ্টি জলের ব্যবহারে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই মুহূর্তে জল সম্পদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।
নিম্নেই জল সংরক্ষণের (conservation of resources water)জন্য পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা হল –
(১) জলাভূমি গুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। জলাভূমি গুলোকে বুঝিয়ে যাতে চাষ জমি তৈরি না হয় বা ঘরবাড়ি তৈরি না হয় তার জন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। জলাভূমির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা দরকার। জলাভূমি গুলি মাটির জল ধারণ ক্ষমতাতে বৃদ্ধি করে। জলাভূমি জাত ও উদ্ভিদ এবং প্রাণিসমূহ সাধারণ মানুষ ব্যবহার করার পরিবর্তে চারপাশে বসবাসকারী মানুষ যাতে জলভূমির সংরক্ষণে উৎসাহিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে ৫০ তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রাকৃতিকভাবে মুজে যাওয়া জলাভূমি গুলির সংস্কার করা দরকার।
(২) বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে অতিরিক্ত জলকে সঞ্চয় করে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা যায়। এর মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেচ ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর নব্যতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই রকম প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৩) যত্রতত্র গভীর ও অ গভীর নলকূপ স্থাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভূস্তরের জলের প্রকৃত মানচিত্র গঠন করে কোন জায়গা থেকে কতটা জল তোলা যেতে পারে তার সঠিক পরিমাপ করে তবে নলকূপ স্থাপন করা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারিগতভাবে উদ্যোগী হতে হবে।
(৪) অথবা ব্যবহার জল যাতে নষ্ট না হয় সেই রকম নাগরিক সচেতনতা প্রয়োজন। অকারণের টেপ থেকে জল পড়ে নষ্ট যাতে না হয় তার দিকে প্রত্যেককে সচেতনতা প্রয়োজন। অকারণে ট্যাব থেকে জল পড়ে নষ্ট যাতে না হয় তার দিকে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।
(৫) সঠিক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োগ প্রণালীর জলকে যাতে শোধিত করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।। জল শোধনকারীর ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে জলকে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ভাসমান পদার্থ সমূহ যেমন কাঠের টুকরো, গাছের পাতা, মৃত জীবজন্তুকে ধাতু নির্মিত চাকরির মাধ্যমে জল থেকে মুক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ভারী ধাতুসমূহকে তিতিয়ে পড়তে দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে পরে জলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি পদার্থ থাকে।
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ৮০০০ লিটার জলে ৪০০ টন নাইট্রোজেন, ১৩৬ টন ফসফরাস এবং ৪৮০ টন পটাশিয়াম থাকে। এই জল খেয়ে পরিমাণমতো মাছ চাষের খামারে প্রেরণ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য পাওয়া গেছে। কলকাতা শহরের নোংরা জলকে এইভাবে কাজে লাগিয়ে শহর সংলগ্ন ভেরি গুলিতে মাছ চাষ করা হয়। ভাসমান জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা ও অন্যান্য বিশেষ কয়েক ধরনের স্যাওলা জল থেকে দূষিত পদার্থ বিশেষ করে ভারী ধাতু শোধনে সাহায্য করে। এই সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে নোংরা পতিত জলকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেকটি শহরে যাতে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
সবশেষে বলা যায় জল সম্পদের প্রকৃত অবস্থাকে সম্মুখ উপলব্ধির মাধ্যমে সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পদটির সুষ্ঠু ব্যবহারের সাহায্য করবে। আগামী দিনে জল সমস্যার সমাধানে সঠিক পদক্ষেপ আগামীদিনের সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।
✍️ জৈব বৈচিত্রা সংরক্ষণ ( conservation of biodiversity introduction)
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে নানান ধরনের , প্রাণী, জীবাণু বসবাস করে বিবর্তনের পথে পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রভাবিত করছি পরস্পরের অস্তিত্বকে। পৃথিবীর মোট জীবের ধরন কত প্রকারের তা আজও জানা যায়নি, কিন্তু এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে আমাদের মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নে এই বৈচিত্র খুবই জরুরী। আমরা এই বৈচিত্রের মধ্যে সৃষ্টির রহস্যের সাধ অনুভবের সাথে সাথে জাগতিক চাহিদার স্বাদও পূরণ করি।
রোগ প্রতিষেধক ঔষধ থেকে শুরু করে বাহারি পোশাক, এসবই আহরণ করি এই বৈচিত্র ভান্ডার থেকে। এসবই জীব বৈচিত্রের ফসল। সুতরাং এই পৃথিবীর বুকে যে বিরাট জীববৈচিত্র বর্তমান তাকে রক্ষা করা আমাদের উচিত। জৈব বৈচিত্র বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের জিন, প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্রের সমাহার।
জীবনের এই প্রত্যেকটি একক প্রকৃতিতে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলে। আপাতদৃষ্টিতে ভূমিকা হীন একটি জীব অপরের টিকে থাকার প্রশ্নে সুদৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই উপলব্ধির ছোঁয়া আমরা প্রথম পাই ২০০ বছর আগে মরিশাস দ্বীপের একটি ঘটনা থেকে। দীপ্তি ছিল জনহীন। ডোডো নামক এক পাখি বাস করত পরম সুখে। জীবনের কোন ঝুঁকি ছিলনা। ওদের ওড়ার দরকারও খুব একটা ছিল না। ধীরে ধীরে এদের ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের লোকেরা এসে বসবাস শুরু করলো ওই নির্জন দ্বীপে। পরে এলো আফ্রিকার আর এশিয়ার খামার শ্রমিকরা। মেতে উঠলো ডোডো পাখি নিধনে। কয়েক বছরের মধ্যেই ডোডো পাখি পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল এক বিশেষ প্রজাতির গাছ যার বীজ বিস্তারে এবং অঙ্কুরোদগম্মে এই পাখির বিশেষ ভূমিকা ছিল।
জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রয়োজন তিন কারণে –
- নৈতিক প্রশ্নে সংস্থার সৃষ্টির কোন কিছুকে ধ্বংস করার অধিকার মানুষের নেই।
- আর্থিক প্রশ্নে – খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি, ঔষধপত্র, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি তৈরির কাঁচামাল প্রভৃতি অর্থকারী জিনিস সমূহ আমরা বিভিন্ন জীব থেকে সংগ্রহ করি।
- বাস্তুতন্ত্রের প্রশ্নে – বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে, আবহাওয়া মন্ডল এর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রশ্নে, পুষ্টি পদার্থের আবর্তনের প্রশ্নে, জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ একান্ত জরুরি।
এপর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মতো। অনুমান করা হয় পৃথিবীতে প্রায় ১ কোটি প্রজাতি বর্তমান রয়েছে। সমুদ্রের থেকে স্থলভাগে জৈব বৈচিত্র্য অধিক দেখা যায়। চির সবুজ বনে সবচেয়ে বেশি জৈব বৈচিত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষ জৈব বৈচিত্রে ধনী দেশগুলির অন্যতম। এই জৈববৈচিত্র আমরা কয়েকভাবে সংরক্ষণ করতে পারি। –
১) পরিবেশের মধ্যে সংরক্ষণ – জৈব সম্পর্কে যখন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সঠিকভাবে টিকে থাকতে এবং বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা হয় তখন এই ধরনের সংরক্ষণ কে পরিবেশের মধ্যে সংরক্ষণ বলে। এই পদ্ধতি জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত এবং আদর্শ। ন্যাশনাল পার্ক, স্যাংচুয়ারি, নেচার রিজার্ভ, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রভৃতি পরিবেশের মধ্যে সংরক্ষণের উদাহরণ।
২) পরিবেশের বাইরে সংরক্ষণ – জীবের বাসস্থানের বাইরে প্রজাতির জনসমষ্টির একটি বিশেষ নমুনা বা বিশেষ কতকগুলি জিন, জিন সমূহ, পরাগরেণু, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু প্রভৃতিকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদ কে এই পদ্ধতিতে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সিডব্যাঙ্ক জিন ব্যাংক প্রভৃতি এই পদ্ধতির উদাহরণ। জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের এই দুই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষে বহু প্রতিষ্ঠান জৈববৈচিত্র সংরক্ষণে এবং উপযুক্ত ব্যবহারের কাজে নিযুক্ত যেমন – বন ও পরিবেশ মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক প্রভৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
৩) সম্পদ বিচক্ষণ ব্যবহার – সম্পদ সমূহের বিচক্ষণ ব্যবহার বলতে আমরা বুঝি সম্পদের চরিত্রকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের যথাসম্ভব কম ক্ষতি করে উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। সম্পদের অতি ব্যবহার এবং অপব্যবহার রোধ করা। এ ব্যাপারে ব্যক্তির সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এভাবেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ (conservation of resource) খুব ভালোভাবে করা যায়।

