environmental ethics means – পরিবেশের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই পোস্টে।
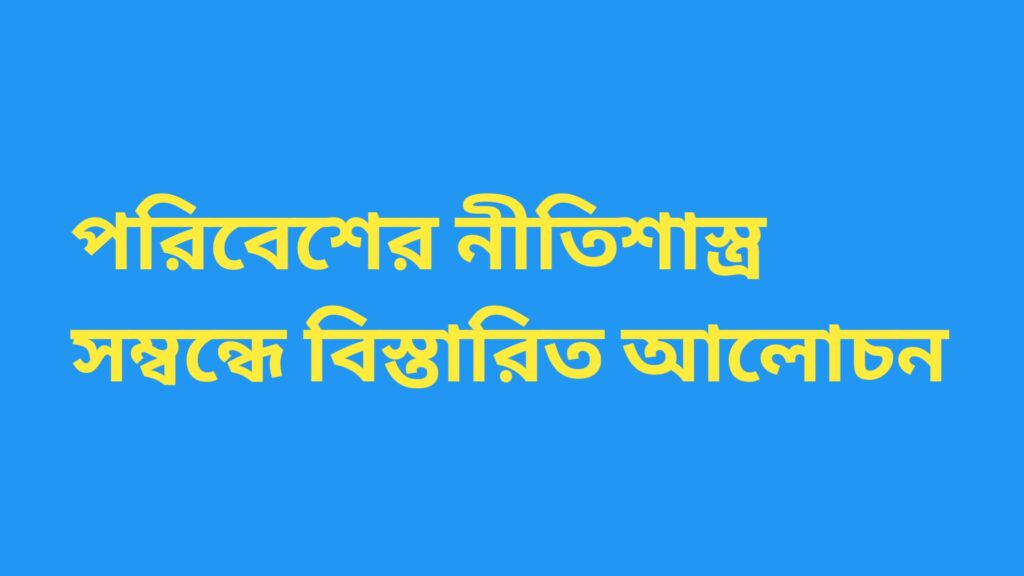
নীতিশাস্ত্রে দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা বিশেষ। যেখানে মানুষের পক্ষে কোন কাজটি করণীয় কোন কাজটি করণীয় নয়, কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন চুরি করা, প্রতারণা করা, অন্যের ক্ষতি করা প্রভৃতি অনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার অন্যের জীবন রক্ষা করা, সততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণাবলী কে নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
নীতি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে বেশিরভাগ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন । যেমন পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন যুদ্ধের সময় শত্রুকে হত্যা করা বা একজন হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া অনৈতিক কাজ নয়। জাতীয় স্বার্থে মিথ্যা বলাকে নৈতিক কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক তা আলাদা আলাদা হয়।
পরিবেশ নীতি শাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত তার নীতিগত দিকসমূহ আলোচনা করা । পরিবেশ নীতি শাস্ত্রে মানুষের কাজকর্ম ও জীবন যাপনের ধরন এবং ব্যাক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশের সাথে সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়।
১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষ এবং স্রষ্ঠার মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক বোঝাতেই নীতিশাস্ত্র ব্যবহৃত হত। কিন্তু যখন মানুষের কৃতকর্মের ফলে পরিবেশ দূষিত হল, অম্ল বৃষ্টি, উষ্ণায়ন ও জল স্তরের ছিদ্র এইরূপ নানা ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করল, তখনই প্রশ্ন উঠল পরিবেশে মানুষের ভূমিকা নিয়ে। এই নিয়ে নানান বিতর্কে সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশ নীতি শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ১৯৭৯ সালে প্রথম এই বিষয়ের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
পৃথিবীর বুকে মানুষের কৃষিজীবী সমাজ গঠিত হল, তারা তাদের পছন্দমত খাদ্যশস্য চাষাবাদ করতে লাগল, গাছপালা কাটতে শুরু করল, মাটিতে লাঙল দিল, গবাদিপশুর চাষ শুরু করলো, তখন থেকেই মানুষ তার ইচ্ছা অনুসারে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে শুরু করল। কিন্তু ধারাবাহিক ও সচেতনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের নেশায় তখন থেকেই মানুষ মেতে ওঠে যখন পশ্চিমে দেশগুলোতে প্রোটেস্টান নীতি শাস্ত্র চালু হয়। যার মূল বক্তব্য মানুষ প্রকৃতি সৃষ্ট জীব সুতরাং সে সর্বোচ্চ সুখ ও সমৃদ্ধি আশা করতে পারে।
এই নীতি প্রাচীন ও ওরিয়েন্টাল ধর্ষণের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, যেখানে বলা হয়েছে এই পৃথিবীর সমস্ত জীব এবং জড় স্রষ্টার সৃষ্টি। মানুষও সেই সৃষ্টির অংশ। পৃথিবীর কোন কিছুকেই সে ধ্বংস করতে পারে না। ঋকবেদ অনেক স্তোস্ত্রে এই গভীর উপলব্ধির কথা আছে।
✍️ পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিকত দৃষ্টিভঙ্গি ( environment ethics )
পরিবেশে মানুষের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এই নিয়ে নীতিগতভাবে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান যথা –
মানুষ্য কেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র – এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি সকল প্রজাতির সেরা সুতরাং যে সর্বোচ্চ সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করবে। পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব থাকবে। পৃথিবীর যা কিছু, সে জৈব বৈচিত্রই হোক বা প্রকৃতির অন্য কোন সম্পদই হোক তা মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে।
প্রকৃতি কেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র – এই নীতি অনুসারে মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ। মানুষ সহ অন্যান্য সকলজীবী সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে অন্যদের থেকে অধিকতর উন্নত হবার কোন কারণ নেই। প্রকৃতিতে সকল জীবেরই নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা আছে। মানুষের প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় কারোর সৃষ্টি হয়নি।
✍️ প্রকৃতি কেন্দ্রিক ও মানস্য কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা
প্রকৃতি কেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস যে এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব বলে কোন কথা নেই। প্রত্যেক প্রজাতিরই বিশেষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের মধ্যে যেমন বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা, নীতি জ্ঞান আছে সেইভাবে চিতা বাঘের শিপ্রগতি বা জোনাকির আলো জ্বালানোর ক্ষমতা আছে যা মানুষের নেই।
আবার মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী আছে সেগুলি বেশি মূল্যবান এই তথ্য মানতেও তারা নারাজ। কারণ মানুষের যে বিশেষ গুণাবলী যেমন বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা, তা বাদ দিলে অন্য প্রাণীর থেকে তার কোন পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে পরিচয়ের জন্য এই গুণগুলি একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে মহৎ বলে কিছু নেই, যেমন ক্ষিপ্রগতিই চিতার বৈশিষ্ট্য।
একটি প্রজাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুলি ছাড়াও যদি অন্য কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারত তাহলে সে আরোও উন্নত হত। যেমন মানুষ যদি চিতার মত গতি সম্পন্ন হতো এবং চিতার যদি মানুষের মতো বুদ্ধি থাকতো। বর্তমানে দেখা গেছে একটি প্রজাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অন্য প্রজাতিতে সঞ্চারিত করা যায় না। চিতাকে মানুষের মতো হাতের ব্যবহার করতে হলে মানুষের নানা বিক গঠন প্রাপ্ত হতে হবে, এবং তখন সে তার নিজের অর্থাৎ চিতা হিসেবে পরিচিতি হারাবে। তাই কোনো বৈশিষ্ট্য এই উন্নত নয়।
অর্থাৎ সকল জিবিই সমান। কেরি বেশি বা কম উন্নত নয়। আমরা যদি পরিবেশ কেন্দ্রিক মতবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিই তাহলে ও দেখতে পাবো সকল প্রজাতি সমান এই মতবাদকে সমর্থন করা যায়।
✍️ মানুষের আত্মরক্ষার ও অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার
মানুষের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমরা দুটি তথ্য পরিবেশন করতে পারি।
মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার – মানুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার ক্ষতিকারক উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে হত্যা করতে পারে। মানুষের নীতিশাস্ত্রে যে আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এই নীতির মিল আছে।
অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার – মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করার জন্য অন্য প্রাণীর প্রাথমিক চারিদিকে বিঘ্নিত করতে পারে। কারণ তা না হলে তার অস্তিত্বের সংকর দেখা দিবে।
ভালোভাবে টিকে থাকতে গেলে প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বন্য প্রাণীর প্রাথমিক চাহিদাকে বিঘ্নিত হলেও নীতি শাস্ত্রে তা অন্যায় নয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে প্রথম বিশ্বের দেশগুলো তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সচেষ্ট, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের প্রাথমিক চাহিদার কথা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।
যাই হোক এই নীতি মানুষের প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে সকল প্রজাতির সমান প্রাধান্যের কথা এখানে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমরা এটুকু চিন্তা করলেই দেখতে পাবো এর সঙ্গে সকল প্রজাতির সমান প্রাধান্যের বক্তব্যের বিশেষ কোনো ফারক নেই। আমরা যদি অন্য প্রজাতিদের স্বার্থে আমাদের প্রাথমিক চাহিদা কি পূরণ না করি তাহলে অচিরে আমরা বিলুপ্ত হব। এবং নীতিগতভাবে আমরা নিশ্চয়তা চাইবো না।
আমরা পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করলেও তার মূল লক্ষ্য কিন্তু আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে মানুষের চাহিদার একটা সীমা আছে, যে সিমার মধ্যে পরিবেশ কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে কোন বিরোধ থাকে না। এই বিষয়টি নিম্নের নীতির দ্বারা আলোচনা করা হল।
👉 অসমসত্বের নীতি
যদি মানুষ তার প্রাথমিক প্রয়োজনব্যাপী সুখী জীবনযাত্রার প্রয়োজনে অন্যের প্রাথমিক চাহিদা কে বিঘ্নিত করে তবে তা পরিত্যাজ্য।
এই নীতি আমাদের জীবনযাত্রা ধরন কে পাল্টে দিতে পারে। সকল প্রজাতির সমান অধিকারের বক্তব্য কি গ্রহণ করতে না পারলে উপরোক্ত নীতি কোনোভাবেই গ্রহণীয় হবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল জীবের সমান গুরুত্বের কথা স্বীকার করছি ততক্ষণ আমাদের সুখছনদের জন্য অপরের প্রাথমিক চাহিদাকে বিঘ্নিত করার কথা ভাবতে পারবো না।
একইভাবে ওপর মানুষের প্রয়োজনকে পূরণ না করে আমরা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার কথা ভাববো না। সমতা বা প্রজাতির মধ্যে সাম্য বলতে আমরা বুঝি অন্য কোন প্রজাতির প্রাথমিক চাহিদা কি বিপন্ন করে মানুষের প্রাথমিক নয় এমন সব চাহিদা পূরণ করা যা কাম্য নয়। সব প্রজাতির সমান অধিকারের নীতি বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার একান্ত চাহিদা এমন কোন কিছুর প্রয়োজন অন্য প্রজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে না, আবার মানুষ নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে অপর প্রজাতির প্রাথমিক চাহিদাকে বাধা দিতে পারে। এবং তার নীতিগতভাবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে আমরা ” Ecological Holism ” এর সাহায্য নিতে পারি।
” Ecological Holism ” এ নীতিগতভাবে দু ধরনের গ্রহণীয় মতবাদ আছে –
প্রথমত, পৃথিবীর সমগ্র জীবন মন্ডল এবং বৃহত্তর পরিবেশ যার মধ্যে আছে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, পাহাড় পর্বত, নদ নদী, অনু পরমানু। একটি প্রজাতির মঙ্গল অথবা একটি বাস্তুতন্ত্রের মঙ্গল বা সমগ্র জীব গুলের ভাল হলে কোন একটি বিশেষ জীবেরও ভালো হবে। যদি মানুষের প্রাথমিক চাহিদা বিপন্ন হয় তাহলে আমরা কোনভাবেই নীতিগতভাবে তাকে কোন ত্যাগ করতে বলতে পারিনা।
মানুষ্য কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরা কোনভাবেই মানতে নারাজ যে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। তাই মানুষের অধিকার আছে সব কিছুর ওপর কৃতিত্ব করার। আমরা এই দাবিকে মানুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করব।
মানুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকেরা সমস্ত জীবের সমান অধিকার মানতে নারাজ। মানুষ শ্রেষ্ঠ কেননা তার মূল্যবোধ সংস্কৃতি এবং উন্নত গুণাবলী যা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।
এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি পরিবেশ কেন্দ্রিক মানুষের বক্তব্যকে। মানুষ অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সমান হোক আর নাই হোক আমাদের নীতিগত অধিকার আছে আমাদের আত্মরক্ষা করার তার জন্য প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কে বিনাশ করতেও হতে পারে। আবার মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন কেউ আমরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদি আমরা ধরে নিই মানুষই শ্রেষ্ঠ তাহলে মানুষেরই নীতিগত কর্তব্য নিজেদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন ইচ্ছা পূরণ না করে অন্য সকলকে রক্ষা করা।
পরিবেশ নীতি শাস্ত্রে তা পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক বা মানুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক। আমাদের দুটি কথা বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত অন্যান্য প্রজাতির প্রাথমিক চাহিদা, আমাদের প্রাথমিক চাহিদা ও আমাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মধ্যে সীমারেখা টানা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য আমরা অন্য প্রাণীর প্রাথমিক চাহিদা কে বিপন্ন করি।
মানুষকে অন্যান্য প্রজাতি অপেক্ষা উন্নত ভাবার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি দৌড় প্রতিযোগিতায় একজন প্রথম এল, পরে দ্বিতীয় জন, তারপরে তৃতীয়জন, তারপরে চতুর্থ । এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রায় সমকক্ষ যদিও প্রথম জনের মতো নয়। উন্নত এই প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অন্য একটি প্রাণী বিশেষ উন্নত। যেমন কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি, ঈগলের দৃষ্টিশক্তি অথবা সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য তৈরীর ক্ষমতা।
মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করলে এগুলির গুরুত্ব বুঝা যায়। সুতরাং পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য যে সকল প্রজাতিরই গুরুত্ব সমান তা সবাই মানতে বাধ্য। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত উভয়কেই শুধু গুরুত্ব দেই তাহলে অন্যান্য প্রজাতির গুরুত্বকে অস্বীকার করব।
বর্তমান পরিবেশ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা একটা কথা বুঝতে পারছি এই প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদান কোন না কোন ভাবে অপরকে প্রভাবিত করছে। মানুষও এই প্রকৃতির একটি উপাদান। অন্যান্য সজীব এবং জড় উপাদান গুলি কোন না কোনভাবে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।
তাই যেহেতু সকল মানুষের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার আছে তাই অন্যান্য পরিবেশের সব উপাদান কেই সংরক্ষণ করা তার দরকার তা না হলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এবং নীতিগতভাবে আমরা নিশ্চয়ই তা চাইব না। তাই মানুষ্যকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার যে মূল কথা মানুষের কর্তৃত্ব, মানুষের অস্তিত্ব, তা রক্ষা করতে গেলে পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার শরিক হতে হবে কারণ প্রমাণিত যে গাছপালা পশুপাখি প্রভৃতিকে বাদ দিলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তো দূরের কথা মানুষ পিকে থাকতেই পারবেনা।
মানুষ যদি উন্নতই হয় , যেহেতু মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ক্ষমতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যে বিবর্তনের পথে অর্জন করেছে তাই তারি কর্তব্য পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা। আনন্দ ও সুখ উপভোগের পদ্ধতি পরিবর্তনের ও ধ্বংস ও আহরণের মধ্যে আনন্দ না উপভোগ করে নিজের ন্যূনতম চাহিদাকে মিটিয়ে প্রকৃতির সুন্দর রাখার মধ্যেই আনন্দ উপভোগ করা।
প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের সঙ্গে প্রত্যেকের যে বন্ধন, প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর যে জটিল প্রক্রিয়া এবং তার ছন্দকে, প্রাণের রহস্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে পরিপূর্ণ এবং উন্নত করে মানসী পারে এই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে। শুধুমাত্র আর্থিক উন্নতি কি প্রগতির মাপকাঠি হিসেবে না ধরে আত্মিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতিও মানুষের একান্ত প্রয়োজন।
✍️ পরিবেশ নীতি শাস্ত্রের নির্দেশাবলী
১৯৮৯ সালের অর্থনৈতিক বৈঠকের পরে ১৯৯৩ সালে bioethics এর ওপর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিবেশ, প্রকৃতির সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল উন্নতির লক্ষ্যে সাধারণের জন্য পালনীয় কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল –
- সমস্ত দিক থেকে স্থিতিশীল উন্নতির ধারণা গ্রহণ করা।
- বাস্তুতন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে নিজ থেকে উপলব্ধি করা এবং পরিবেশের বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করা এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা।
- অন্ত এবং বহিভাগের পরিপূর্ণ হিসাব করা।
- পারস্পারিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরিবেশের মূল্যায়ন করা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার জন্য এবং পরিবেশের নিজের জন্য।
উপরের নীতিগুলি কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে –
- জীব মন্ডলের উপযুক্ত কার্যকারিতার জন্য পরিবেশের যে কার্যপ্রণালী তাকে রক্ষা করা উচিত।
- আর্থসামাজিক উন্নতির সাথে সাথেই পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষণ করা।
- শিক্ষা গবেষণা ও তথ্য পরিবেশন এর মাধ্যমে পরিবেশকে ভালো করে জানা।
- পৃথিবীর সাধারণ সম্পদ সমূহ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সমঝোতা সৃষ্টি করা।
- দ্বিমত যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিষেধ মূলক নীতি গ্রহণ করা।
বিস্তারিতভাবে যে সকল নির্দেশাবলী ব্যক্তি, সমষ্টি, সরকার ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মেনে চলার জন্য দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ –
- পরিবেশগত যে কোন বিষয়ের প্রভাব গুলি ব্যক্তি, সমষ্টি, উন্নতি এবং প্রকৃতিতে কি তা প্রত্যেকের খতিয়ে দেখা উচিত।
- প্রতিনিয়ত পরিবেশের মান নির্ধারণ করা এবং গ্রহীত তথ্য যাতে করে সকলে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- সামাজিক, সংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক প্রতিটি বিষয়ের উপর পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- প্রযুক্তির শর্তহীন হস্তান্তর।
পরিবেশ নীতিতে দুই ধরনের মতাবলম্বী মানুষ দেখা যায়। প্রথম দল মানুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গোক্ষন করে এবং যাদের মূল বক্তব্য হল, এই পৃথিবীর বুকে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব তাই প্রকৃতি তার ভালোর জন্য তার ইচ্ছেমতোই ব্যবহার হবে। পরিবেশ কেন্দ্রিক মানুষেরা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব মানতে নারাজ। তাদের মতে প্রত্যেক প্রাণীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা তার সক্রিয় এর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পরিবেশের প্রত্যেকের গুরুত্বই সমান, প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে।
আপাতদৃষ্টিতে এই দুই মতবাদের মধ্যে বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হলেও এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষ উন্নত জীব বলে তারিখ কর্তব্য হওয়া উচিত পরিবেশকে পরিবেশের সমস্যা কে উপলব্ধি করা, এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, এবং এসব কিছু তার নিজের টিকে থাকার স্বার্থে। কারণ পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান অন্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের আত্মরক্ষন ও অস্তিত্বের প প্রশ্নে মানুষের এসব কিছু করা উচিত এবং অতিস্বাচ্ছন্দেরমুহে অন্য প্রজাতির প্রাথমিক চাহি দিকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়।
পরিবেশ নীতি শাস্ত্রের উপজীব্যকে ব্যক্তি, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উপলব্ধি করতে হবে।
প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিক মূল্যায়ন, প্রকৃতির কার্যপ্রণালী কে উপলব্ধি করা, বাচা এবং বাঁচতে দেওয়ার নীতি পরিবেশের নীতিবিদ্যার মূল উপজীব্য। প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারে কিন্তু চাহিদা কে নয়। এই বিষয়টা আমাদেরকে কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে।

